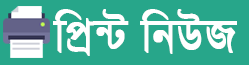
এবি অপু :
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন শব্দ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু — “সেইফ এক্সিট”। হঠাৎ করেই এই শব্দটি এমন এক আতঙ্ক, কৌতূহল ও রটনার মিশেলে পরিণত হয়েছে যে, অনেকে এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তবের চেয়ে বেশি কল্পনায় বাস করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—“সেইফ এক্সিট” আসলে কী? এটি কি রাজনৈতিক আত্মরক্ষা, নাকি নৈতিক দেউলিয়ার প্রতিচ্ছবি?
🔹 ১. সেইফ এক্সিট মানে পালানোর মনস্তত্ত্ব
কোনও সমাজে যখন মানুষ বা নেতৃত্ব পালানোর পথ খোঁজে, তখন বোঝা যায়—আত্মবিশ্বাসের জায়গাটি ফাঁপা হয়ে গেছে। “সেইফ এক্সিট” ধারণাটি মূলত এক ধরনের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ—যেখানে নিজের অতীত সিদ্ধান্তের দায় এড়িয়ে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান চলে।
কিন্তু ইতিহাস বলে, যে নেতৃত্ব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার জন্য পৃথিবীর কোথাও আসলে নিরাপদ প্রস্থান থাকে না। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে বিদেশি দূতাবাস বা ভিসা তাকে রক্ষা করবে, তবে সেটি এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।
🔹 ২. ভিসা আর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব
অনেকে মনে করেন—বিদেশি ভিসা, রেসিডেন্স পারমিট বা ইনভেস্টমেন্ট স্কিম থাকলে সংকটের সময় দেশ ছাড়াটা সহজ হবে। বাস্তবতা উল্টো।
বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই কেবল “ভিসা আছে” বলেই কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় না। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ইউরোপীয় দেশগুলো কূটনীতিতে আবেগ নয়, কড়াকড়ি নীতিতে চলে। তাদের এম্বাসিগুলো নিজেদের নাগরিক ছাড়া আর কারও জন্য ‘সেইফ এক্সিট’ বা আশ্রয়ের দরজা খুলে রাখে না।
অন্যদিকে এলিট বা ইনভেস্টমেন্ট ভিসা ক্যানসেল করা আজকাল খুব সহজ—বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিকদের ক্ষেত্রে। ফলে যাঁরা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মনে করছেন, বাস্তবে তাঁরা ঝুঁকির মুখেই আছেন।
🔹 ৩. “সেইফ এক্সিট” আলোচনার রাজনীতি
“সেইফ এক্সিট” শব্দটি এখন শুধু নিরাপত্তার নয়, ক্ষমতার ভাষাও বটে।
যারা ক্ষমতার মঞ্চে বসে আছেন, তারা জানেন—ক্ষমতা হারানো মানে প্রভাব হারানো। আর তাই অনেকে আগেভাগে সরে যাওয়ার পথ খোঁজেন, কেউবা গোপনে বিদেশে বিনিয়োগ করেন।
কিন্তু জনগণ জানে—এই পালানো কৌশল আসলে দায়িত্ব এড়ানোর আরেক রূপ।
একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে নেতৃত্ব পালায় না, জবাব দেয়; দায় এড়ায় না, জবাবদিহি করে।
🔹 ৪. জনগণ ও রাষ্ট্রের বাস্তব শিক্ষা
এই “সেইফ এক্সিট” আলোচনাই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতার ঘাটতি কত গভীর।
যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হয় যে নেতা বা কর্মকর্তা নিজের নিরাপত্তার জন্য পালানোর চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে হবে—ব্যবস্থাটির ভেতরেই ভয় আছে, ভাঙন আছে।
একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রে কারও পালানোর দরকার হয় না; কারণ ন্যায়বিচার সবার জন্য সমান।
কিন্তু যখন ন্যায় শুধু নির্বাচিতদের সুরক্ষা দেয়, তখন সেইফ এক্সিটই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র ভরসা।
🔹 ৫. আগেভাগে পালানো নয়, আগেভাগে ঠিক করা দরকার
যারা এখন ভাবছেন—সময় এলে “চলে যাবো”, তাদের জন্য ইতিহাসে শিক্ষা আছে।
সংকটের দিন এলে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়, বিমানবন্দর থেমে যায়, এবং তখন ‘সেইফ এক্সিট’ বলে কিছু আর থাকে না।
তাই পালানোর চিন্তার বদলে এখনই আত্মসমালোচনার সময়—কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যেখানে মানুষ নিজ দেশেই নিরাপত্তাহীন বোধ করে?
পালানোর আগেই রাষ্ট্রটিকে ঠিক করা জরুরি। কারণ সেইফ এক্সিট যদি সবার লক্ষ্য হয়, তাহলে কারও জন্যই সেফটি থাকবে না।
🔹 ৬. আমাদের যা শেখা দরকার
“সেইফ এক্সিট” নিয়ে এই জাতীয় আতঙ্ক আমাদের একটা কথা স্পষ্ট করে বলে—আমরা এখনো জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করতে পারিনি।
রাষ্ট্র যখন নাগরিককে ভয় দেয়, নাগরিক তখন পালানোর পথ খোঁজে।
কিন্তু গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকে, যখন নাগরিকরা পালিয়ে নয়—দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার দাবি করে।
তাই সেইফ এক্সিট নয়, সেইফ সোসাইটি গড়াই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য—যেখানে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও মানবিক আস্থা থাকবে; যেখানে কোনও নাগরিকের পাসপোর্ট নয়, তার বিবেকই হবে নিরাপত্তার প্রতীক।


